বাংলাদেশের জনগণ এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক অর্জন দেখাল। সূচনায় চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলন, পরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের বন্ধুর ও ঝুঁকিপূর্ণ পথ অতিক্রম করে দেশের সবচেয়ে প্রলম্বিত স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটালেন শিক্ষার্থীরা। আওয়ামী লীগ সরকারের শোষণ, নির্যাতন, দুর্নীতি যতটা তীব্র ছিল, ঠিক একই তীব্রতায় তার পতনও ঘটল। দলটির জনসমর্থন, সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান একেবারেই তলানিতে এখন এবং এটি জনগণই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হাসিনা সরকারের পতনের পর প্রথাসিদ্ধ বিজয় মিছিল না হলেও মানুষের আবেগ-উচ্ছ্বাস, স্লোগানে স্লোগানে রাজপথ প্রকম্পিত করা এবং অন্যান্য আবেগময় মুহূর্ত আমাদের চোখে আজীবন জ্বলজ্বল করবে। দেশবাসী এটির নাম দিয়েছেন ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান। তবে এ ধরনের কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের পর মানুষের এমন ঢল আমরা আগেও দেখেছি, দেখেছি এরশাদ সরকারের পতনের পরও। আমরা বিজয়ে-পতনে উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের বাঁধভাঙা জোয়ার লক্ষ করি।
যে তরুণ প্রজন্ম ও জনগণ মুক্ত-অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় এনেছিল, তারা ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪-এর নির্বাচনে নিদারুণভাবে আশাহত হন। এদেশে নির্বাচন হচ্ছে গরিবের উৎসব। কিন্তু গত তিনটি উৎসবে তারা যোগদান করতে পারেননি। আমাদের নির্বাচনের ইতিহাসে ‘সূক্ষ্ম কারচুপি’, ‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’-এসব পদবাচ্য উদ্ভাবনের পথ ধরে যুক্ত হয়েছে রাতের ভোট বা ‘নৈশভোট’, ‘আমি আর ডামি’, ‘স্বতন্ত্র’(!) ইত্যাদি পদবাচ্য। এসব কারণে জনগণের বারবারই আশাভঙ্গ হয়েছে। শেখ হাসিনা যখন বলতেন, ‘রাতে কোনো ভোট হয়নি’; তখন মানুষ এ মিথ্যাচার শুনে আর কোথাও গিয়ে দাঁড়ানোর জায়গা পেতো না। এভাবে নৈতিক ও মানসিকভাবে জনগণ এক শূন্যতার গহ্বরে নিপতিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে জনগণ এ শূন্যতা কাটিয়ে ওঠে জেনারেশন জেডের কল্যাণে ও উদ্যোগে, ৫ আগস্টের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

এই যে এত বড় একটি বিজয় অর্জিত হলো, তারপর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠা উচিত-একজন শাসক কেন স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে? এ প্রশ্নের উত্তরে অনেক বিষয় সামনে এসে দাঁড়ায়-যদি একজন শাসক ব্যক্তিগতভাবে লোভী, ক্ষমতালিপ্সু ও কর্তৃত্ববাদী হন; যদি সংবিধানে তাকে এ সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে; যদি উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি এরূপ একটি সুযোগ গ্রহণের পথ পেয়ে যান; যদি সে দেশের নাগরিক ও বুদ্ধিজীবীরা তার কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠার পথকে আরও সুগম করে দেন ইত্যাদি। এসব কারণে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নটি এখন ঘুরেফিরে আসছে, যদিও রাষ্ট্র সংস্কারের প্রসঙ্গটি প্রথম উত্থাপিত হতে শুনি ২০০৯ সালে। এখন কেউ বলছেন রাষ্ট্র সংস্কার, কেউ বলছেন রাষ্ট্র মেরামত। আসলে রাষ্ট্র কোনো কাঠের আসবাব নয় যে এটিকে ‘মেরামত’ করতে হবে। তাই যথাযথ শব্দই প্রয়োগ করা উচিত, যেমন ‘রাষ্ট্র সংস্কার’।
একজন শাসক তখনই কর্তৃত্ববাদী বা ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠেন, যখন তিনি অথবা তার স্তাবকরা লক্ষ করেন সংবিধান বা আইনে তার সেই ভিত্তি তৈরি করা আছে। আমাদের সংবিধানে একজন ব্যক্তি কতবার প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন, তার সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়নি। সংবিধানের ৫৬(১) অনুচ্ছেদে বিধৃত আছে, ‘একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী থাকিবেন।’ এ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করা হয়েছে। একই ব্যক্তি কতদিন এ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন, তারও কোনো দিকনির্দেশনা এ অনুচ্ছেদে নেই। একই পদে দীর্ঘদিন অধিষ্ঠিত থাকার সুযোগ তার মনে অন্ধের মতো একটি প্রতিক্রিয়া ঘটায় যে, জনগণ তাকে চাইছে; অতঃপর তিনি তার ক্ষমতাকে আরও সংহত করার জন্য আইন, সংবিধান, বিধানাবলী একের পর এক সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আমাদের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় বলে কাজটি অনেক সহজ হয়ে যায়। এ জন্য সংবিধানের এতদসংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসহ ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের দাবি দীর্ঘদিনের। ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন সংসদ-সদস্য নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করলে সংসদে তার আসন শুধু শূন্যই হবে না, পরবর্তী কোনো নির্বাচনেও তিনি সংসদ-সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন না। এহেন অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে রাষ্ট্রে বিরাজমান থাকে, সেখানে শাসক অতি সহজেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারেন। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় সাধারণত দলীয় প্রধানরাই হন সরকারপ্রধান। অথচ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোয় (যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য) একজন যেমন দুবারের অধিককাল সরকারপ্রধান হিসাবে থাকতে পারেন না, তেমনি দলীয় প্রধানকেই যে সরকারপ্রধান হতে হবে, এমন কোনো নিয়মও নেই। যুক্তরাজ্যে ক্ষমতায় আসীন একজন প্রধানমন্ত্রীকে অযোগ্য মনে হলে সহজেই তাকে পদচ্যুত করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশে নজিরবিহীন ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো, সে সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা আকাশচুম্বী, যদিও এ সরকারের আইনগত স্বীকৃতি নেই, কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটি বিগত স্বৈরাচারী সরকার ২০১১ সালে একতরফাভাবে বাতিল করে দিয়েছে। তবে জনগণের ইচ্ছাই আইন, একথা সুবিদিত। এ জনগণই আশা করে, সরকার নাগরিকদের প্রতিটি কথা, প্রস্তাবনা ধৈর্য ধরে শ্রবণ করবে, যা কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো কখনো করে না।
বদলে যাওয়া বাংলাদেশে এ সরকারের মেয়াদ কতটা দীর্ঘ হবে, তা পরিষ্কার করা হয়নি। সংসদ ভেঙে দেওয়ার পর ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করে জনগণকে তাদের পছন্দসই প্রার্থী বাছাইয়ের সুযোগ দিয়ে তাদের সরে পড়া উচিত। এ সরকারের মেয়াদ শেষ হলে কোনো উপদেষ্টা পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অতীতেও তা-ই হয়েছিল। সরকারে দুজন আন্দোলনকারী ছাত্র প্রতিনিধি রয়েছেন, যদিও তারা ওয়াচডগের দায়িত্ব পালন করবেন বলে প্রত্যাশা ছিল। তাদের যেসব সহযোদ্ধা-বন্ধু এখনো আন্দোলনোত্তর সার্বিক পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারে ব্যাপৃত রয়েছেন, তারা এ দায়িত্বটিও পালন করবেন আশা করি।
সংবিধান সংস্কার না করে রাষ্ট্র সংস্কার সম্ভব নয়। এজন্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির রেওয়াজ রয়েছে। অতঃপর জাতির ম্যান্ডেট নেওয়ার জন্য রেফারেন্ডাম বা গণভোটের আয়োজন করা এখন সময়ের দাবি। দ্রুতই আন্দোলনকারী শক্তিগুলোর সঙ্গে সংলাপ করে সরকারের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার রূপরেখা প্রণয়ন করা উচিত। জনগণের নাড়ি ও হৃদস্পন্দন অনুধাবন করে বোঝা যায়, ইতিহাসের জঘন্যতম জুলাই গণহত্যার বিচারের লক্ষ্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং দুর্নীতি ও লুটপাটের বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ পথকে নিষ্কণ্টক রাখার জন্য সব ধরনের নিষ্ঠুর ও অমানবিক কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিচারের দাবি উপেক্ষা করার কোনোই সুযোগ নেই। জনগণের মনে রাষ্ট্র সংস্কারের যে আকাঙ্ক্ষা ইতোমধ্যেই জাগরুক হয়ে উঠেছে, তার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য আইন, বিচার, শাসন বিভাগ ও সংবিধানের ক্ষমতা কাঠামোর বিষয়ে টাস্কফোর্স গঠন এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে গণ-আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। এসব কাজ এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে। তারপরই গণভোটে অনুমোদিত হওয়া সংবিধানের অধীনে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা যুক্তিযুক্ত হবে।






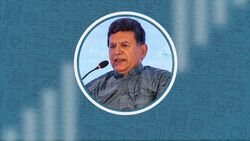

















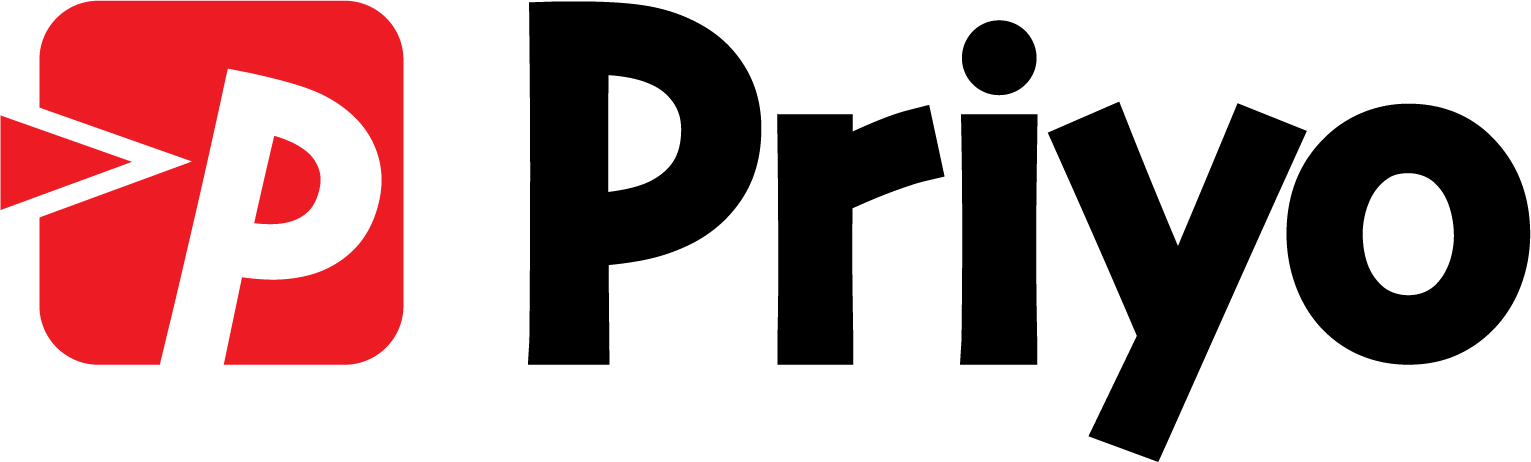 News
News