বাংলাদেশের প্রথম উচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরও একটু ‘বয়স্ক’ হলো। পৃথিবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস মাপতে গেলে, এই বয়সকে অবশ্য অনেক নস্যি মনে হবে। তবু ‘সামান্য’ এ বয়সেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ইতিহাস, তা নিতান্তই ক্ষুদ্র নয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জাতিগঠনে পীঠস্থানের ভূমিকা পালন করে এসেছে শতবর্ষ ধরে।
এ কথা বলাবাহুল্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান, যার চৈতন্যের অন্দরে জন্ম হয়েছে বাংলাদেশ নামের জাতিরাষ্ট্রের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রতিষ্ঠান, যাকে অনুসরণ করে বাংলাদেশের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও উচ্চ বিদ্যাপীঠ নিজেদের গড়ে তুলেছে। এটুকু অবদান দূরে সরিয়ে রেখে, ভাবার প্রয়োজন আছে, ঠিক কী অবস্থায় আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এ দেশের উচ্চশিক্ষার কাঠামোটি?
আরও সুনির্দিষ্টভাবে, স্বাধীনতার প্রায় ৫৫ বছর পর, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এবং সমাজ-রাষ্ট্রে ঠিক কী অবদান এই বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবস্থা রাখতে পেরেছে বা পারছে, তা নিয়ে আলাপ তোলা জরুরি হয়ে পড়েছে।
শিক্ষার চিন্তাপদ্ধতি
বাংলাদেশের শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা বহুল চর্চিত। কিন্তু শিক্ষার চিন্তাপদ্ধতির সমস্যা নিয়ে চর্চা প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু সনদধারীই শিক্ষিত বা বিদ্বান, সনদহীন-অজ্ঞাতমাত্রই অশিক্ষিত বা অবিদ্বান—এটি একটি ভয়ংকর ঔপনিবেশিক সমস্যাক্রান্ত প্রকল্প। এই প্রকল্প মানলে আমাদের চিরভাস্বর প্রবাদ-কন্যা বিদুষী খনাকে ‘অবিদ্বান’ বলে খারিজ করা যায়। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সেটি কতটা যৌক্তিক হবে?
১৮৩৫ সালে ভারতের ভাইসরয় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের প্রশ্রয়ে টমাস বেবিংটন মেকলে এ প্রকল্পের জন্মদাতা, কেননা তাঁর ‘অভিধানে’ শিক্ষা মানেই প্রাতিষ্ঠানিক উপযোগিতা ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজ তৈরি করা। এর হাতিয়ার (টুল) হিসেবে মেকলে সাহেব খুব সচতুরভাবে যোগ করে দিলেন ভাষাকে, মানে ইংরেজিকে। ইংরেজি হয়ে উঠল ভারতবর্ষের ‘আধুনিক’ ও পাশ্চাত্যমুখী শিক্ষার বাহন (মিডিয়াম অব ইনস্ট্রাকশন) ও সরকারি ভাষা। ফলে চাকরির বাজারে ঢুকতে হলে ইংরেজি জানা জরুরি হয়ে উঠল।
বিনয় ঘোষ তাঁর বাংলার বিদ্বৎসমাজ গ্রন্থে এই চিন্তাপদ্ধতির সমালোচনা করে বলেছেন, ভারতীয় তথা বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্তের প্রথম ইংরেজি জানার দৌড় পকেট ডিকশনারিতে টুকে রাখা কয়েক ডজন ইংরেজি শব্দ। এর অগ্রভাগে ছিল ‘ইয়েস, নো, ভেরি ওয়েল’ এবং তাতেই সে নিজেকে সাহেবের কাছারিতে চাকরি বাগিয়ে নেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করতে শুরু করে দিয়েছিল।
শুধু তা-ই নয়। সে ভাবতে থাকল, মনিবের যোগ্য ভৃত্য আমি, এ ধরাধামে আমার চেয়ে উত্তম চাকর আর কে আছে! চাকরি সে চাকর সত্তার ভাবাদর্শ থেকেই করেছে, অহমিকা হিসেবে যোগ হয়েছে মাতৃভাষার অক্ষরজ্ঞান ও ইংরেজি ভাষার ‘ইয়েস-নো-ভেরি ওয়েলে’র ওপর দখল। মুখ্যত, সনদ-সংস্কৃতিকে বিদ্যাশিক্ষার ‘একক ফড়িয়া’ (সোল এজেন্ট) বানানো হয়েছে যে বাজারের স্বার্থে, সেই বাজারের ডাকনামই হচ্ছে চাকরি।
আরও গভীরভাবে দেখলে, শিক্ষা গ্রহণ মানে আদতে ‘শিক্ষিত’ হওয়াও নয়, চাকরি করার প্রাথমিক শর্ত পূরণ করা। অর্থাৎ চাকরি করার যোগ্য তিনিই, যিনি সনদধারী-শিক্ষিত। এভাবেই শিক্ষা হয়ে উঠল চাকরির সমানুপাতিক। ফলে যিনি কৃষক বা শ্রমিক, তাঁর বিশেষায়িত কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অস্বীকৃত রয়ে গেল এবং তিনি হয়ে উঠলেন শ্রেণি-আধিপত্যের মর্মন্তুদ শিকার।
■ শিক্ষা গ্রহণ মানে আদতে ‘শিক্ষিত’ হওয়াও নয়, চাকরি করার প্রাথমিক শর্ত পূরণ করা। অর্থাৎ চাকরি করার যোগ্য তিনিই, যিনি সনদধারী-শিক্ষিত।
■ শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শিক্ষা মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তের কাছে শৌখিন কোনো বিষয় নয়। এ হলো তার অর্থ উপার্জন ও ‘গাড়ি-ঘোড়ায় চরা’র দরজা।
যে কৃষক শ্রমে-ঘামে ফসল ফলান, যে শ্রমিক কলকারখানায় উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, সে কৃষক বা শ্রমিকের জ্ঞান ‘অপাঙ্ক্তেয়’। কেননা তিনি প্রথাগত শ্রেণিকক্ষ-সংস্কৃতির অংশ হতে পারেননি কখনো। আফসোস! আজও শিক্ষার চিন্তাপদ্ধতির এ নীতিবোধই সমাজ ও রাষ্ট্রকে খামচে ধরে রেখেছে।















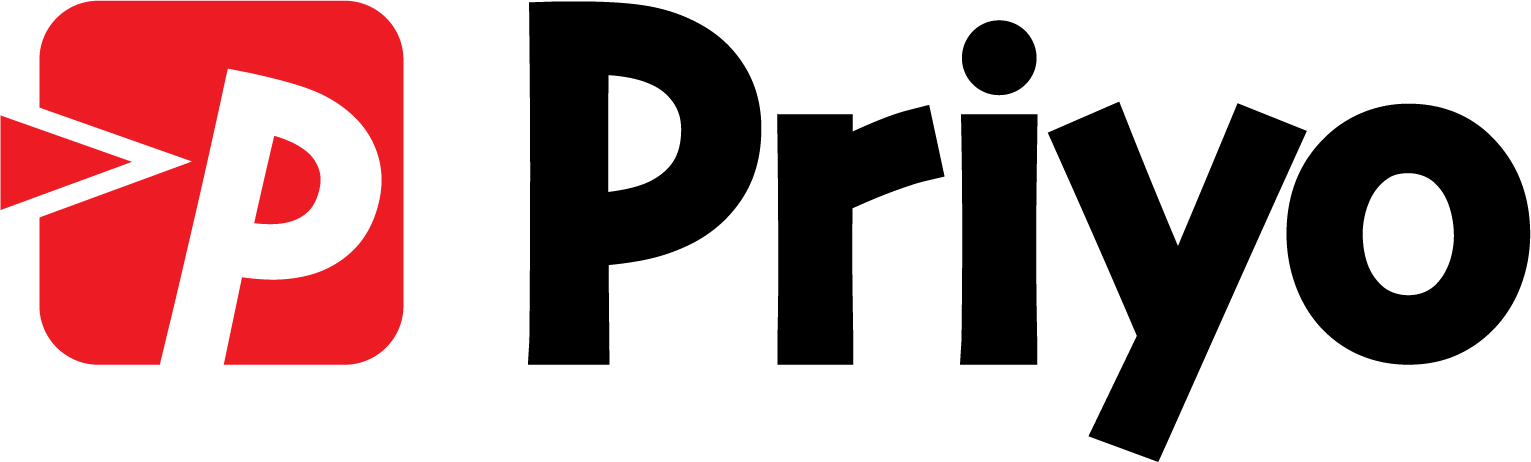 News
News