রোগীর নিত্য সহচর একাকিত্ব। পরিবার, সমাজ, বিশ্ব থেকে বিচ্যুতি যেন অসুখের একমাত্র গন্তব্য। একজন রোগী, মনোরোগী সবল হতে পারে না। সে হতে পারে না সৃষ্টিশীল। ১৯১২ সালের ‘লুনাসি অ্যাক্ট’ ডিক্রির মতো এদের একমাত্র গন্তব্য নির্বাসন– সমাজ থেকে, জীবন থেকে, শিল্প-সাহিত্য থেকে। অথচ জীবনের কঠিনতম সময়ে, সংগ্রামের সময়ে মানবচিত্ত এমন এক পরিশুদ্ধির পথ অতিক্রম করে, পারগেটরি দিয়ে যাত্রা করে, যে নিপুণতম সৃষ্টির জন্য তার মন তখন প্রস্তুত থাকে। রোগগ্রস্ত, বিষণ্ন অথবা শোকার্ত মানুষের কাছে জীবন যখন একজন কারাবন্দির অভিজ্ঞতা মাত্র, তখন সাহিত্য আর শিল্প জীবনের জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে থাকে। অপেক্ষায় থাকে উদ্গিরণের। তবে এটি মানতে হবে, জগতের মহান সাহিত্যিক কিংবা চিত্রকরের সৃষ্টির পেছনে হয়তো জীবনসংগ্রাম জড়িত ছিল না। নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রে অসীম প্রতিভাবান ছিলেন, যেমন ছিলেন দা ভিঞ্চি আর পাবলো পিকাসো। তাদের প্রতিভার পাত্র এতটা পূর্ণ ছিল যেন তার স্ফুরণে হয়তো কোনো বিশেষ ব্যক্তি, ঘটনা বা দুর্ঘটনার দরকার পড়েনি। তবে এমন অনেক প্রতিভাধর মানুষ রয়েছেন, যাদের আবির্ভাবের পেছনে, প্রতিভার উদ্গিরণের পেছনে একটি বিশেষ ট্রিগার কাজ করেছে। মনোরোগ কিংবা জীবনের কঠিনতর সংগ্রাম থেকে পরিত্রাণ বা নির্বাণের প্রয়াসে হলেও কি সৃষ্টিশীলতায় আশ্রয় নেওয়া যায় না?
প্রখ্যাত মেক্সিকান চিত্রকর ফ্রিডা কাহলোর নাম মনে আসছে। অষ্টাদশী ফ্রিডা একটি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। ফলাফল দীর্ঘ দুই মাসের হাসপাতাল পরবাস। ফ্রিডার মেরুদণ্ড ভেঙেছিল তিন জায়গায়, ডান পা ১১ জায়গায়, স্থানচ্যুত হয়েছিল তার ঘাড়, ভেঙেছিল কলারের হাড়। মৃত্যুর সঙ্গে করমর্দনের এমন পরাবাস্তব অভিজ্ঞতার পর তিনি যখন বন্দি হাসপাতালের কক্ষে; আত্মমুক্তির আশায় ফ্রিডা ভরসা রাখেন রং-তুলিতে। নিশ্চল ফ্রিডা বিছানার ওপর আয়না টাঙিয়ে, তার মন ও কল্পনার সমস্ত বল একত্রিত করে আত্মপ্রতিকৃতি তৈরিতে মন দেন। সৃষ্টি হতে শুরু করে একের পর এক অসাধারণ চিত্রকর্ম। জন্ম হয় একজন মহান চিত্রশিল্পীর।
যে কোনো রোগীর হারাবার ফর্দ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। প্রথমে সে হারায় স্বাস্থ্য, সচলতা; এর পর যুক্তি, চিন্তাশীলতা; তারপর নিদ্রা, প্রিয়জন, কখনও গোটা পরিবার, সবশেষে সমাজ। রোগীর পৃথিবীতে সেবা আছে, সুস্থতা নেই; ওষুধ আছে, স্বাভাবিকতা নেই। রোগী তাই বিচ্ছিন্ন এক সমান্তরাল পৃথিবীর নাগরিক, যার অদৃশ্য দেয়াল ভেদ করে সুস্থদের জীবনে অনুপ্রবেশ মানা। অসুখের কারাগারে আবদ্ধ রোগীরা নিঃসঙ্গ। রোগ হতে পারে শারীরিক বা মানসিক। প্রায় সব রোগীর গন্তব্যই যেন নিঃসঙ্গতা। সমাজ নিশ্চিত করে– যেন হাসপাতাল কক্ষের জানালা দিয়ে এক টুকরো আকাশের চেয়ে বেশি কিছু তার দৃষ্টিগোচর না হয়। পরিবার নিশ্চিত করে– যেন সেবার পাশাপাশি করুণার পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ থাকে রোগীর জন্য।
কেবল রোগ বা মনোরোগই নয়, স্বজন হারানোর শোকযাত্রাতেও আমরা নিঃসঙ্গ। আমাদের দেশে না রয়েছে কোনো সাপোর্ট গ্রুপ, না গ্রিফ কাউন্সেলিং। শোক পালনে আবার সময়সীমা বেঁধে দিই আমরা। সমাজ বলে– চার থেকে সর্বোচ্চ ৪০ দিন, এর পর ফিরতে হবে স্বাভাবিক কোলাহলে। শোকেরও যে একটা নিজস্ব গতি আছে; ব্যক্তির শোক যে একান্তই তার নিজের; নিজের মতো করে পালন করা একটি অধ্যায়– তা স্বীকার করতেও সমাজের কষ্ট হয়। আমাদের দেশে শোকের কোনো আউটলেট নেই। শোকের সময় রান্না বন্ধ। বন্ধ বিনোদন। বন্ধ বন্ধুবাৎসল্য। শোক থাকবে একাকী, নিঃসঙ্গ অন্ধকার ঘরে নীরবে পতিত অশ্রুর মতো।
রোগ, মনোরোগ বা শোক, ব্যক্তিজীবনের সংগ্রাম মোকাবিলায় আমরা কোনো ‘অ্যাকশনেবল’ উপায় বাতলে দিই না। উৎসাহ জোগাই না এ অবস্থাকে সহনীয় করতে। পশ্চিমে রোগী, মনোরোগী বা শোক পালনকারীকে মনের অনুভূত আবেগ প্রকাশে সৃষ্টিশীল একটি মাধ্যম খুঁজে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। জার্নাল লেখা, ছোটগল্প বা উপন্যাস রচনা, রোগীর মানসিক মুক্তির একটি উপযুক্ত পথ বলে প্রমাণ করেছে মনোবিজ্ঞান। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ক্রিস্টিন হার্টল লেখালেখির সঙ্গে মানসিক মুক্তির সরাসরি সম্পর্কের প্রমাণ দিয়েছেন। এ জন্যই পশ্চিমে ক্যান্সার সার্ভাইভার বা মনোরোগ অতিক্রমকারী রোগীরা বেস্ট সেলিং গ্রন্থ রচনা করেন, চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন কিংবা চিত্রকর্মের প্রদর্শনী দেন।
আমাদের সমাজে সৃষ্টিশীলতা, মুক্তচিন্তার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো চর্চাই নেই। সব ছাত্রছাত্রীই পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বরের প্রত্যাশায় প্রস্তুতি নেয়। সফল ছাত্ররা বিজ্ঞান আর প্রকৌশল বিদ্যার দিকে ঝোঁকে। সাহিত্য, দর্শন এখন প্রথম সারির কেউই পড়তে চায় না। এসব বিষয়ে নাকি চাকরির মন্দা। এই সমাজে রোগী, মনোরোগী কিংবা শোকযাত্রী, অর্থাৎ দুর্বলের আবার সৃষ্টিশীলতা থাকতে আছে কি? তাদের জন্য রয়েছে কেবল করুণা, অমনোযোগ; নিদেনপক্ষে সমান্তরাল অসুস্থ সমাজের স্টিগমা।



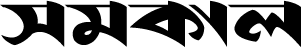











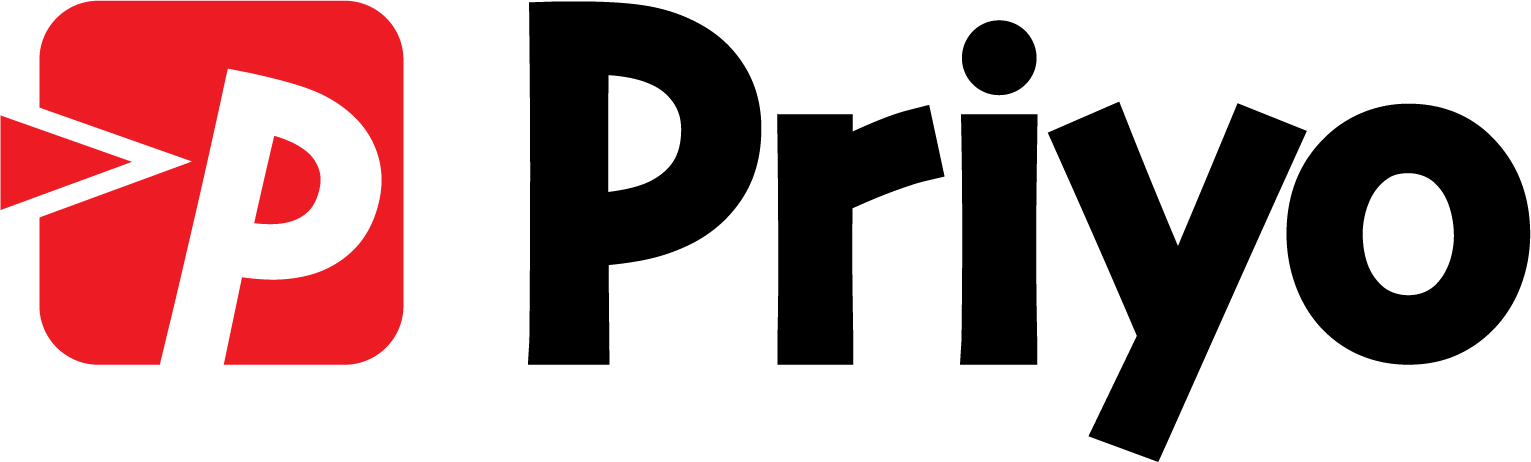 News
News