চিলমারী থেকে কুড়িগ্রামে আসছিলাম সিএনজিতে। ড্রাইভারসহ ছয়জন। ড্রাইভার রফিকুল ইসলাম (৩৫) ও পাশে বসা মঞ্জু ভাই (৫২)—দুজনেই করোনার সময় গ্রামে এসেছেন, আর ফিরে যাননি। চিলমারীর পানাতিপাড়া গ্রামের মঞ্জু ভাই কোনাবাড়ী, গাবতলি এলাকায় রিকশা ও ভ্যান চালাতেন। বললেন, ‘প্রয়োজন নাই, তাই ঢাকায় ফিরি নাই। বাড়িতেই কাজকাম আছে। ঢাকায় আয় যেমন, খরচাও তেমন। ঢাকায় একটা মানুষ খাইতে ৩০০ টাকা নাগে। আর গ্রামোত ৩০০ টেকা বাজার কইরলে ৭–৮ জনে খাওয়া যায়।’
রফিকুল ইসলামের ২ ছেলে। বাড়ি রংপুরের কাউনিয়ায় পূর্ব চানহাটে। তিনি কেন ঢাকায় ফিরলেন না, জানতে চাইলে বলেন, ‘অসুস্থ ছিলাম, তারপর গাড়ি কিনলেম। ঢাকায় আয়–রোজগার ভালো হইলেও ওখানে তো ফ্যামিলি নাই। এখানে ফ্যামিলির সঙ্গে আছি।’ এগুলোই হচ্ছে সাধারণ গল্প। সবার গল্প। করোনা শহরের মুখোশ খুলে দিয়েছে।
মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে ঠাঁই দিয়েছে গ্রাম। করোনাকালে গ্রাম আবার নিজেকে প্রমাণ করেছিল। কেউ কেউ অতীতের ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হওয়ার নিন্দা করবেন। কিন্তু অতীতকে কেবল নেতিবাচক বলে উপস্থাপন করাটা ওই কথিত ভাবালুতার চেয়ে বিভ্রান্তিকর।
কুড়িগ্রাম জেলা। বলা হয়, এটি নাকি দারিদ্র্যের শীর্ষে। আর এর পেছনের বড় কারণ হিসেবে বলা হয়, এই জেলার অধিবাসীরা ‘কুড়িয়া’ (অলস)। অন্যান্য জেলায় গড় প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা যেখানে লাখখানেক, সেখানে এ জেলায় মাত্র হাজার দশেক। কেন তারা দেশের বাইরে যেতে অনাগ্রহী?
দারিদ্র্যের একটি বড় সূচক ধরা হয় হাতে টাকা না থাকা। কুড়িগ্রামের প্রায় সবারই বড় পরিসরে নিজস্ব বাড়ি আছে। গৃহহীন মানুষ কম। নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রায় সব ফসলই এখানে ফলে। যে পানি ও বাতাস তারা ভোগ করেন, তা তো টাকায় কিনতে পাওয়া যায় না।
শিশু ও বয়োবৃদ্ধদের আনন্দিত জীবন যাপনের পর্যাপ্ত অবসর আছে। ফলে শহরের মানসিক বৈকল্যে তাঁরা ভোগেন না।
অর্ধশতাধিক নদ–নদীর যে সুস্বাদু মাছ তারা ভোগ করে তা উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তুলনীয়। চরাঞ্চলের শিশুরা হয়তো শহরের শিশুদের মতো বই পড়তে পারে না। কিন্তু তারা প্রত্যেকে সাঁতার জানে, প্রচুর গাছের নাম জানে। এমনকি কোন গাছের কোন ফলের স্বাদ কেমন, কোন রোগে কোন উদ্ভিদ কাজে লাগে—এসবও তাদের জানা।















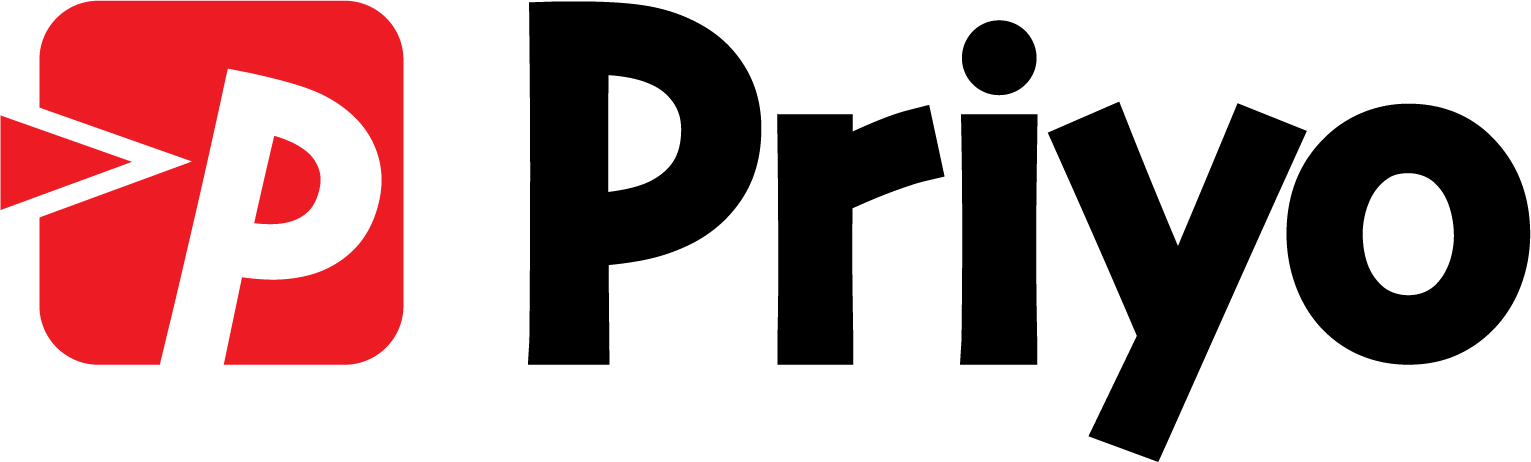 News
News